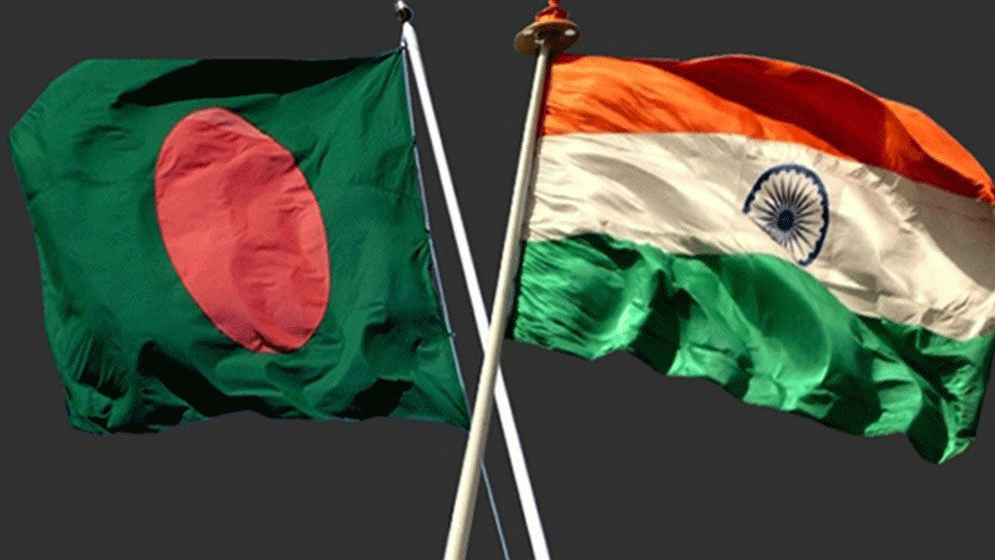প্রবাস বাংলা ভয়েস ডেস্ক :: বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দেড় বছর ধরে চলমান বৈশ্বিক করোনা মহামারিতে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রমাণিতভাবে প্রায় সাড়ে ১৮ কোটি মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং প্রায় ৪০ লাখ মানুষ এ ভাইরাসের আক্রমণে মারা গেছেন। ল্যাবরেটরি পরীক্ষার বাইরে আরও কত মানুষ যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, সেটি হিসাব করে বলা যাচ্ছে না। তবে সেই সংখ্যা ল্যাবরেটরিতে প্রমাণিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
একদিকে করোনা থেকে মুক্ত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা, করোনায় আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ করে মরে যাওয়ার ভীতি, করোনার ছোবলে আপনজনদের মৃত্যু, করোনা হলে সঠিক চিকিৎসা পাওয়ার অনিশ্চয়তা-এসব নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষগুলো যখন এক ভয়াবহ মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তখন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এসেছে করোনার কারণে ঘরবন্দি জীবন, লকডাউন, শিশুর স্কুল বন্ধ থাকা এবং তাদের শিক্ষার অনিশ্চয়তা, চাকরি চলে যাওয়া, ব্যবসা হারানো, দৈনন্দিন আয়ের উপায় বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। বিশ্বব্যাপী একসঙ্গে এ রকম ভয়াবহ অবস্থা স্মরণকালে আর দেখা যায়নি।
প্রাপ্তবয়স্করা যখন এ অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন পার করছেন, তখন শিশুর কী অবস্থা, সেটি একটু আলোচনা করা যাক। দেড় বছর ধরে পৃথিবীর সব দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে বা খুব সীমিত পরিসরে চালু আছে অনলাইনে এবং কিছু কিছু দেশে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থার ভেতর শিক্ষার্থীদের সরাসরি উপস্থিতির মাধ্যমে। তার ওপর করোনার কারণে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, পার্ক, সিনেমা, খেলার মাঠ, মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, বিনোদনকেন্দ্র-এগুলোও বন্ধ বা সীমিত হওয়ার কারণে শিশু, বিশেষ করে শহরের শিশু হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ ঘরবন্দি। যেসব সচ্ছল পরিবারের শিশু কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট পাচ্ছে, তারা সারা দিন পড়ে আছে অনলাইনে গেম, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং এ বয়সে অগ্রহণযোগ্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট নিয়ে। আর শহরের শিশুর মধ্যে যাদের এ সুযোগ নেই, তারা যে কীভাবে তাদের দিনরাত এ বন্দি অবস্থায় কাটাচ্ছে-সেটি একটা গবেষণার বিষয় হতে পারে।
শিশুর জন্য দেড় বছর ধরে এ বন্দি অবস্থা যে কী ভয়াবহ রকম কষ্টের এবং মানসিক যন্ত্রণার, সেটি ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শিশু-কিশোর সংশোধন কেন্দ্র, এতিমখানা বা জেলখানায়ও অন্য মানুষ থাকে, যাদের সঙ্গে কথা বলা যায়, কম্পাউন্ডের ভেতর হাঁটাচলা করা যায়; কিন্তু ঘরবন্দি অবস্থায় তো সেটিও সম্ভব হয় না। কারণ, করোনার ভয়ে কারও বাসায় যাওয়া যায় না, কাউকে বাসায় আনা যায় না, ঘরে কোনো অনুষ্ঠান করা যায় না, কোথাও যাওয়া যায় না, দিন-রাত একই ঘরের ভেতর পরিবারের একই সদস্যদের সঙ্গে আটকে থাকতে হচ্ছে। শিশুর সার্বিক করুণ এ অবস্থাটা কি আমরা অভিভাবকরা সঠিকভাবে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারছি?
এ রকম অবস্থায় দেশে শহরের অধিকাংশ স্কুল, বিশেষ করে প্রাইভেট স্কুলগুলো অনলাইনে ক্লাস নেওয়া শুরু করেছে গত এক বছর ধরে। একটু সচ্ছল পরিবারগুলো তাদের শিশুদের অনলাইন ক্লাস করার জন্য হয়তো কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ করে দিতে পেরেছে; কিন্তু শিশুদের একটা বিশাল অংশকে অনলাইন ক্লাস করতে হচ্ছে অভিভাবকদের স্মার্টফোন ব্যবহার করে, যা তাদের চোখ এবং ব্রেনের ওপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করছে। আর স্কুলগুলোও সব কোর্স কমপ্লিট করার জন্য এমন কঠিন শিডিউল করে ক্লাস নেয় যে, এ শিশুগুলোকে প্রতিদিন গড়ে ৫-৭ ঘণ্টা অনলাইন ক্লাস করতে হয়। তার ওপর আছে ক্লাস টেস্ট, মাসিক পরীক্ষা, কোয়ার্টারলি পরীক্ষা, ফাইনাল পরীক্ষা এসব। করোনা আর লকডাউনের জাঁতাকলে পিষ্ট শিশুদের ওপর এই রকম বিরামহীন মানসিক চাপ যে কী নিষ্ঠুর ‘অত্যাচার’, সেটা কি স্কুলগুলো এবং আমরা অভিভাবকরা সঠিকভাবে বুঝি বা বুঝতে চাই? গ্রামাঞ্চলের শিশু পড়াশোনার ব্যাপারে কী করছে এ দেড় বছর ধরে, তার কোনো পরিসংখ্যান বা গবেষণা তথ্য আমি জানি না।
একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমার এক আত্মীয়ের ছেলে, যার মা-বাবা দুজনই উচ্চশিক্ষিত এবং ছেলেটি ঢাকায় একটি খ্যাতনামা বেসরকারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। এ শিশুটি খুবই ভদ্র এবং মা-বাবার সব কথা শোনে। করোনা ক্রাইসিস আসার আগে থেকেই শিশুটির মা তার একমাত্র সন্তানের ‘ভালো রেজাল্ট’ করার জন্য পড়াশোনা নিয়ে ছেলেটির ওপর মোটামুটি চাপ প্রয়োগ করতেন এবং ছেলেটি তার মায়ের আশা পূরণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টাও করত। করোনা ক্রাইসিস আসার পর যখন স্কুল বন্ধ হয়ে গেল এবং অনলাইনে ক্লাস শুরু হলো, তখন শিশুটির মা স্কুল বন্ধ থাকায় সন্তানের পড়াশোনার ‘ক্ষতি’ পূরণ করার জন্য নিজেই সেই দায়িত্ব নিলেন; অর্থাৎ অনলাইনে ক্লাস করার পরও পড়াশোনা নিয়ে ছেলের ওপর চাপ প্রয়োগ দ্বিগুণ করে দিলেন।
এর ফলাফল দেখা গেল দ্রুত। প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা স্মার্টফোনে অনলাইন ক্লাস করার পর শিশুটি যখন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়, তখনই শিশুটির মা এক গাদা হোমওয়ার্ক এবং প্র্যাকটিসের বোঝা নিয়ে এসে ছেলেটির ওপর চাপিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য-‘ভালো রেজাল্ট’ করা। মাস দুয়েক এ অমানবিক মানসিক চাপ সহ্য করার পর অবশেষে ছেলেটি হাল ছেড়ে দিয়ে পড়াশোনা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল এবং কোনোভাবেই আর শিশুটিকে পড়তে বসানো গেল না। সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রইল মোবাইল ফোনে গেমস নিয়ে। তার ওপর এ অল্প বয়সে পড়াশোনা নিয়ে অধিক মানসিক চাপের কারণে শিশুটির নানা রকম শারীরিক উপসর্গ দেখা দিল-পেট ব্যথা, বমি ভাব এসব। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ছেলেটি যখন বাসায় থাকে, তখনই কেবল ওর পেট ব্যথা এবং বমি ভাব হয়। বাসার বাইরে গেলে এবং বেড়াতে গেলে ওর আর এ উপসর্গ থাকে না। বেড়ানো শেষ করে বাসায় ঢোকার পরই আবার ওর পেট ব্যথা এবং বমি ভাব শুরু হয়।
পেট ব্যথা আর বমি ভাবের জন্য শিশুটিকে ডাক্তার দেখানো হলো। বেশকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার শিশুটির তেমন কোনো শারীরিক সমস্যা পেলেন না। হাইপার অ্যাসিডিটির একটা ওষুধ, কৃমির একটা ওষুধ আর ভিটামিন প্রেসক্রিপশন করে দিলেন। এ ওষুধ খেয়ে শিশুটি দুই-এক দিন ভালো ছিল (খুব সম্ভবত মানসিকভাবে উজ্জীবিত হয়ে)। তারপর আবার সেই আগের উপসর্গ দেখা দিল। এখন তার মা-বাবা কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। এ রকম প্রচুর উদাহরণ আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে আছে; যেখানে শিশু সন্তানদের প্রতি মা-বাবার অতি এক্সপেকটেশনের চাপে শিশু একসময় প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং তাদের জীবনের স্বাভাবিক ট্র্যাক থেকে সরে যায়। এটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।
একজন শিশুর কাছে তার সবচেয়ে বেশি আস্থা এবং নির্ভরতার জায়গা হলো সেই শিশুর মা-বাবা। সেই মা-বাবা যদি শিশুটিকে না বোঝে, শিশুটির সুখ-দুঃখ, কষ্ট, চাওয়া-এগুলো না বোঝে, শিশুটির কষ্টের সময় আপনজন হিসাবে শিশুটির পাশে না দাঁড়ায়; তাহলে সেই শিশু তার কষ্টের কথা কাকে বলবে? কোথায় গিয়ে সেই শিশু মানসিকভাবে একটু স্বস্তি পাবে? অনেক অভিভাবকই এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন; কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে, আগে সুস্থ শরীর এবং মন, তারপর পড়াশোনা, ক্যারিয়ার আর বাকি সবকিছু। জীবনে ভালো কিছু করতে হলে কি খুব বেশি পড়াশোনা করতে হয় বা খুব ভালো রেজাল্ট করতে হয়? মানবসভ্যতার ইতিহাসে যেসব মানুষ দারুণভাবে সাকসেসফুল হয়েছেন এবং সভ্যতাকে পজিটিভভাবে পরিবর্তন করে গেছেন, তাদের অধিকাংশেরই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল না; এমনকি অনেকেই সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। কাজেই পড়ালেখা করলেই সবাই জীবনে উন্নতি করবে এবং দেশ-সমাজের জন্য ভালো কাজ করবে-এটা টার্গেট করে সন্তানদের বড় করার চেষ্টা করা কতখানি যুক্তিযুক্ত, তা ভেবে দেখা দরকার।
সুনাগরিক এবং উন্নত চিন্তা আর দক্ষতার মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সন্তানদের অবশ্যই যথাসম্ভব ভালো এবং উন্নত পড়াশোনা করানোর চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সেটি করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আমি এবং আমার সন্তান এক মানুষ না; ওরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জেনেটিক কম্পোজিশনে জন্ম নেওয়া। ভিন্ন সময়, ভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং ভিন্ন সভ্যতায় গড়ে ওঠা মানুষ। কাজেই সন্তানকে নিয়ে আমার স্বপ্ন এবং সন্তানদের নিজস্ব স্বপ্ন, মূল্যবোধ ও সার্বিক ক্ষমতা একই রকম হবে, সেটা ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়। আর সেরকমই যদি হতো, তাহলে রবীন্দ্রনাথের সন্তানরা রবীন্দ্রনাথের মতোই বিখ্যাত কবি হতেন, আইনস্টাইনের সন্তানরা আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী হতেন এবং বিল গেটসের সন্তানরা বিল গেটসের মতো সফল আইটি ব্যবসায়ী হতেন।
আসল কথা হলো, শিশুর মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করতে হবে, যেন সে তার নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য এবং সারা পৃথিবীর জন্য সম্পদ হিসাবে গড়ে ওঠে; কারও বোঝা বা ক্ষতিকর মানুষ হিসাবে নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ডিগ্রি হলো এ প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা মাত্র উপাদান। বাকি অনেক কিছুই প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি এবং ‘ভালো রেজাল্ট’-এর বাইরে। আজ আমি আমার শিশুর সঙ্গে যে রকম আচরণ করব, তারা সেই রকম আচরণই শিখবে এবং ভবিষ্যতে তারা আমার সঙ্গে এবং অন্যদের সঙ্গে সেই রকম আচরণই করবে।
আমি যদি আমার শিশুসন্তানদের প্রতি সংবেদনশীল হই; তাদের সুখ, কষ্ট, স্বপ্ন, হতাশা-এগুলো উপলব্ধি করে তাদের পাশে বন্ধুর মতো তাদের আপনজন হই, তাহলে ওরাও বড় হয়ে আমার সঙ্গে, পরিবার এবং সমাজের অন্যদের সঙ্গে সেই রকম আচরণ করবে, এমন সম্ভাবনাই বেশি। আর আমি যদি ওদের সঙ্গে স্বার্থপরের মতো শুধু আমি যা ভালো মনে করি, তা ওদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিই; ওদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-এগুলোর কথা চিন্তা না করি, তাহলে ওরা তো বড়ো হয়ে আমার আজকের এ আচরণই আমার প্রতি এবং অন্যদের প্রতি দেখাবে। আমি এবং আমরা কি তখন তাদের সেই স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর আচরণ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারব?
ভবিষ্যতে সুস্বাদু আম খেতে চাইলে বর্তমানে সুস্বাদু আম গাছের চারা লাগিয়ে সেই গাছের যত্ন নিতে হবে। বর্তমানে বেলগাছ লাগিয়ে ভবিষ্যতে আম পাওয়া যাবে না-একেবারে সহজ হিসাব। কাজেই আমরা যদি চাই, আমাদের সন্তান বড় হয়ে ভদ্র, সৎ, বিবেকবান, দয়াশীল, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং দায়িত্বসম্পন্ন মানুষ হবে, তাহলে সন্তানদের সঙ্গে তাদের ছোটবেলা থেকেই আমাদের এসব আচরণ দেখাতে এবং শেখাতে হবে। বেত দিয়ে পিটিয়ে ‘গাধা’কে ‘মানুষ’ বানানোর সেই যুগ এখন আর নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীর মানবসভ্যতায় আছি। আমাদের ‘সেই সময়’ আর আমাদের সন্তানদের ‘এই সময়’-এর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কাজেই আমাদের ‘সেই সময়ের’ তত্ত্ব দিয়ে ‘এই সময়ের’ সন্তানদের গড়ে তোলা যাবে না- এ সত্যটা আমরা যত দ্রুত বুঝব, ততই আমাদের জন্য, আমাদের সন্তানদের জন্য, সমাজ ও দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে।
ডা. শাহীন রায়হান : একটি জার্মান সংস্থার সঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ানদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রোগ্রামে কর্মরত
প্রবাস বাংলা ভয়েস/ঢাকা/ ৩০ আগস্ট ২০২১ /এমএম