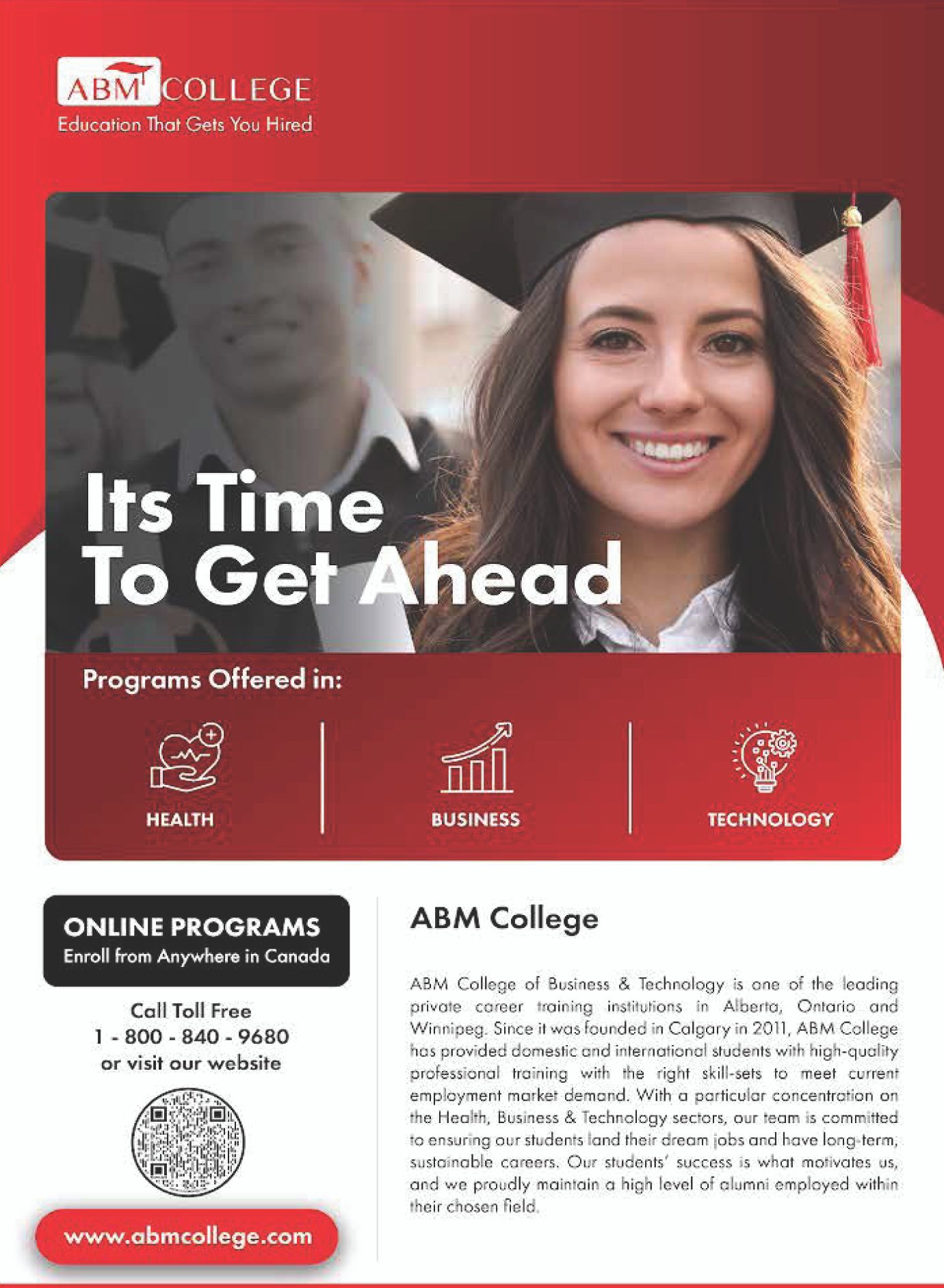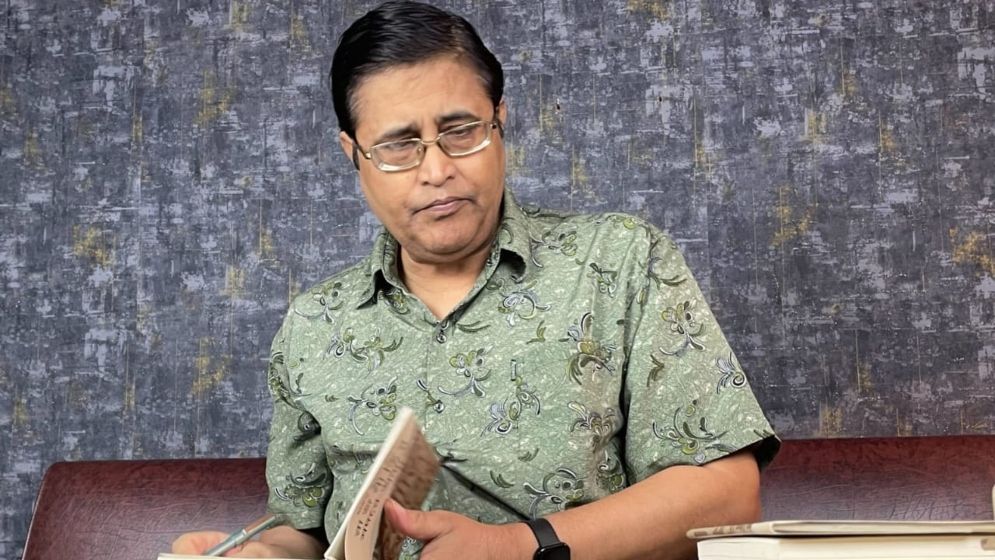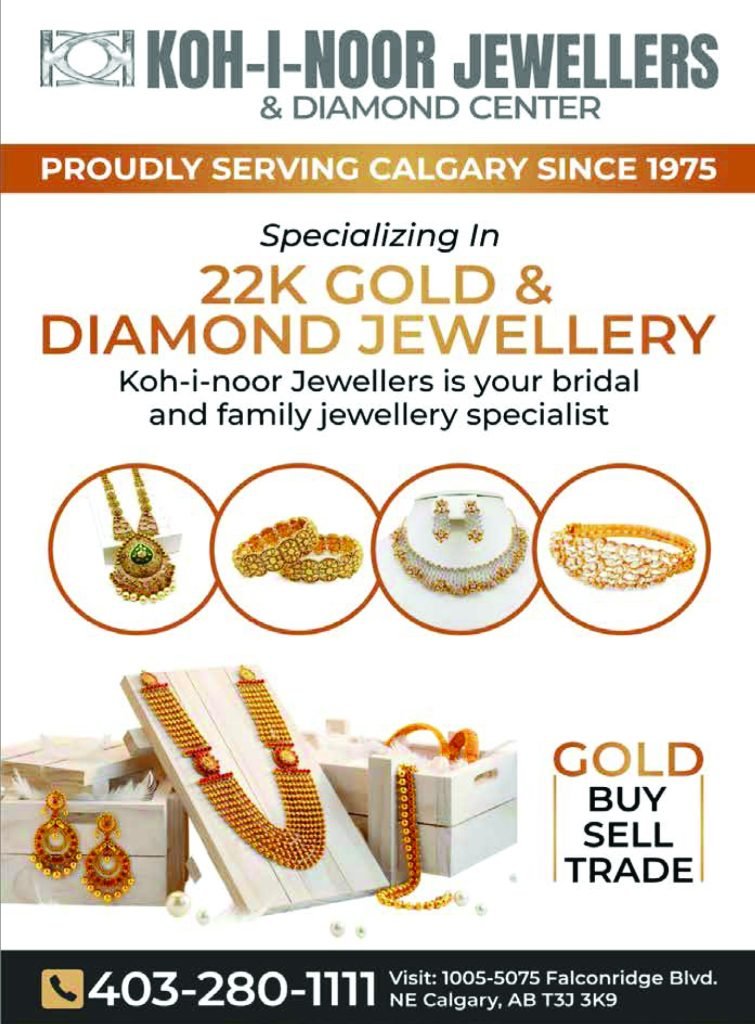বাংলানিউজসিএ ডেস্ক :: আবুল মনসুর আহমদের প্রধান পরিচিতি সুসাহিত্যিক হিসেবে। অনেকেই তাকে আখ্যায়িত করেন ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’-এর মনসুর আহমদ নামে। বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তোলার সুযোগ নেই।
কারণ বাংলা সাহিত্যে ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ একটি অনন্য সাহিত্যকর্ম, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল; জটিল রাজনৈতিক সময়ের এক স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। তবে জেনে রাখা ভালো, অনেকের কাছে রম্য সাহিত্যিক হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত আবুল মনসুর আহমদ একজন সমাজ সচেতন রাজনীতিবিদ ছিলেন।
আওয়ামী মুসিলম লীগের সাবেক সহসভাপতি, হক মন্ত্রিসভার (১৯৫৪) স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লেখালেখির বাইরেও তার একটি গৌরবোজ্জ্বল কর্মজগৎ আছে; সেটি সাংবাদিকতা। ব্রিটিশ ভারতে এই বাংলায় সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রেখে আবুল মনসুর আহমদ তৈরি করেছেন স্বকীয় ধারা; যা অনেক সময় অলক্ষ্যেই আলোচনার বাইরে থেকে যায়।
আবুল মনসুর আহমদের সাংবাদিকতা জীবন শুরু ১৯২৩ সালে ‘ছোলতান’ পত্রিকায়। ওই সময় কলকাতার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মাওলানা মনিরুযজামান ইসলামবাদীর ‘ছোলতান’-এ সহসম্পাদক হিসেবে তিনি কাজ শুরু করেন; বেতন মাত্র ৩০ টাকা।
এর আগে তিনি আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাপ্তাহিক ‘মুসলিম জগৎ’-এ কিছুদিন কাজ করেন। এই পত্রিকাতে তিনি ‘ছহি বড়ো তৈয়বনামা’ নামের একটি রাজনৈতিক রম্য ও ‘সভ্যতার দ্বৈত শাসন’ নামে নামে দার্শনিক-রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেন, যা ওই সময় কলকাতার মুসলিম সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে।
এরপর তিনি যোগ দেন সাপ্তাহিক ‘মোহাম্মদী’তে। এই পত্রিকাতেই আবুল মনসুর আহমদ যথাযথ সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করেন। এখানে তাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। প্রচুর লেখালেখি, সহসম্পাদনা আর নানারকম দায়িত্বের মাধ্যমে তিনি সাংবাদিকতার নানা বিষয় রপ্ত করেন। ওই সময় সপ্তাহে অন্তত ২টি করে উপসম্পাদকীয় লিখতে হত মনসুর আহমদকে।
বিবেচনায় রাখতে হবে, ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের বিংশ শতাব্দীর ২০-এর দশক ছিল অন্যরকম এক সময়। ১৯০৬ সালে ঢাকার আহছান মঞ্জিলে এক ঘোষণায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর এই সময় কলকাতাকে কেন্দ্র করে মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ পর্ব চলছিল। ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হিন্দু সমাজের পাশাপাশি নানা ধরনের মুসলিম সংগঠন, সভা, সমিতি ইত্যাদি সক্রিয় ভূমিকা রাখতে শুরু করে।
বলা যায়, হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিমরাও সাংগঠনিকভাবে রাজনৈতিক সত্তা নির্ধারণে বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠে। ওই সময়টাতে সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে মুসলিম প্রধান পত্রপত্রিকার লেখাগুলো ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ বা কলাম নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতো মুসলিম তরুণ-যুবাদের সভা-সমিতিতে। মুসলিম সমাজের এই জাগরণের প্রেক্ষাপট জায়গা করে নিয়েছিল আবুল মনসুর আহমদের লেখনীতে।
তিনি ‘মোহামম্মদী’তে দক্ষতার সঙ্গে উদ্দীপক শব্দ ব্যবহার করতেন। সাম্রাাজ্যবাদবিরোধী ওইসব লেখায় তিনি ব্যবহার করতেন ‘রক্তচক্ষু’, ‘বজ্রমুষ্টি’ ‘সিংহ নিনাদ’ প্রকৃতির শব্দ; আর তাতে থাকত যুক্তিপূর্ণ কথামালার সমাহার। আবুল মনসুর আহমদের এসব লেখা তৎকালীন ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’র রিডিং রুমে একজন পাঠক জোরে জোরে শব্দ করে অন্য শ্রোতাদের জন্য পড়তেন।
‘মোহাম্মদী’র পর ‘দি মুসলমান’ ও ‘খাদেম’ হয়ে আবুল মনসুর আহমদ যোগ দেন দৈনিক ‘কৃষক’ পত্রিকায়। কৃষক ছিল বড় পরিসরের পত্রিকা। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে এই পত্রিকাটি প্রকশিত হয়। ‘কৃষক’ ছিল মূলত নিখিল-বঙ্গ-কৃষক-প্রজা সমিতির মুখপত্র। একজন সাংবাদিক ও সম্পাদক মনসুর আহমদ সাংবাদিকতাকে আপন করে নিয়েছিলেন। সংবাদপত্র বা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সবার প্রতি ছিল তার বিশেষ নজর।
ওই সময় পত্রিকার কম্পোজিং বিভাগ আজকের মতো এত আধুনিক ছিল না; বরং বলা যায়, অনেক প্রতিকূল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেই সময় কম্পোজিং-এর কাজ করতে হতো। বদ্ধ ঘরে, কালিতে মাখামাখি হয়ে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ছিল তাদের কর্মক্ষেত্র।
মনসুর আহমদ তাদের এই কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম কোনো সম্পাদক, যিনি কম্পোজিং বিভাগে ফ্যান দিয়েছিলেন; যাতে তারা একটু স্বস্তির পরিবেশে কাজ করতে পারে। ছোট্ট এই সিদ্ধান্তের কারণে তিনি সে সময় কলকাতায় বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। আবুল মনসুর আহমদ শুধু একজন সংবেদনশীল হৃদয় নিয়ে সাংবাদিকতা করেননি; এই পেশা তথা সাংবাদিকতাকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়।
ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা পত্রিকায় তিনি রীতিমতো বিপ্লব ঘটান। তার এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল দৈনিক ‘ইত্তেহাদ’ (১৯৪৭) পত্রিকার মাধ্যমে। এই পত্রিকা প্রকাশে মূল ভূমিকা ছিল উপমহাদেশের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। একটি লিমিটেড কোম্পানির অধীনে এই পত্রিকার অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন নবাবজাদা হাসান আলী চৌধুরী ও ফারুকুল ইসলাম। তারা তিনজনই এই পত্রিকা প্রকাশসহ নানা বিষয়ে আবুল মনসুর আহমদকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। এই পত্রিকায় ছিল নিজের মতো করে কাজ করার সুবিধা।
এদিকে নানা ঘটনায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা মনসুর সাহেব এই পত্রিকাকে সাজাতে পেরেছিলেন নিজের মতো করে; সেখানে ফলও আসে খুব দ্রুত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দৈনিক ‘ইত্তেহাদ’ বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। প্রচারসংখ্যা পুরাতন অন্য পত্রিকাগুলোর থেকে দুই থেকে তিনগুণ বেড়ে যায়। এই পত্রিকার সাফল্যের পেছনে বেশ কয়েটি কারণ ছিল। পত্রিকাটি ওই সময়টিকে ধরতে পেরেছিল; ধরতে পেরেছিল পাঠকের আকাক্সক্ষা।
আবুল মনসুর আহমদ জানতেন, সাংবাদিকসহ অফিসের নানা স্তরের কর্মীরাই সংবাদপত্রের প্রাণ। তাই সব সময়ই তিনি তাদের আর্থিক দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করতেন। ইত্তেহাদের আগের পত্রিকাগুলোয় তিনি সাংবাদিকদের বেতন বৃদ্ধির নানা চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি খুব একটা সফল হননি। ফলে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী কর্মী সাংবাদিকতা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যান।
ইত্তেহাদে যেহেতু তিনি প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা পেয়েছিলেন, তাই সেটাকে কাজে লাগিয়ে সাংবাদিক ও অন্য কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করেন। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি একটি যথাযথ কাঠামো দাঁড় করান, যাতে উপকৃত হয়েছে সাংবাদিক সমাজ।
আবুল মনসুর আহমদের সাংবাদিকতা জীবনের শেষ হয় ১৯৫০ সালে। ‘ইত্তেহাদ’ই ছিল তার শেষ কর্মস্থল। প্রকৃতপক্ষে দেশ ভাগের পর কলকাতা থেকে আর পত্রিকাটি প্রকাশের সুযোগ ছিল না।
এরপর তিনি ঢাকায় ফিরে পুরোদস্তুর রাজনীতি শুরু করেন, যে অঙ্গনেও তিনি সাংবাদিকতার মতোই ছিলেন বেশ সফল। গতকাল ৩ সেপ্টেম্বর ছিল সাংবাদিকতা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র আবুল মনসুর আহমদের ১২১তম জন্মদিন, যার বর্ণাঢ্য সাংবাদিক জীবন নিয়ে আজও নানামুখী আলোচনা হয়। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন সাংবাদিকতায় সেই সময়ের উজ্জ্বল এক বাতিঘর, যিনি শুধু তার সমসাময়িক সময়েই আলো ছড়াননি; আজও বাতিঘর হয়ে সাংবাদিকতা পেশাকে পথ দেখাচ্ছেন পেশাদারিত্ব ও উৎকর্ষতার।
বাংলানিউজসিএ/ঢাকা/ ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯/ এমএম