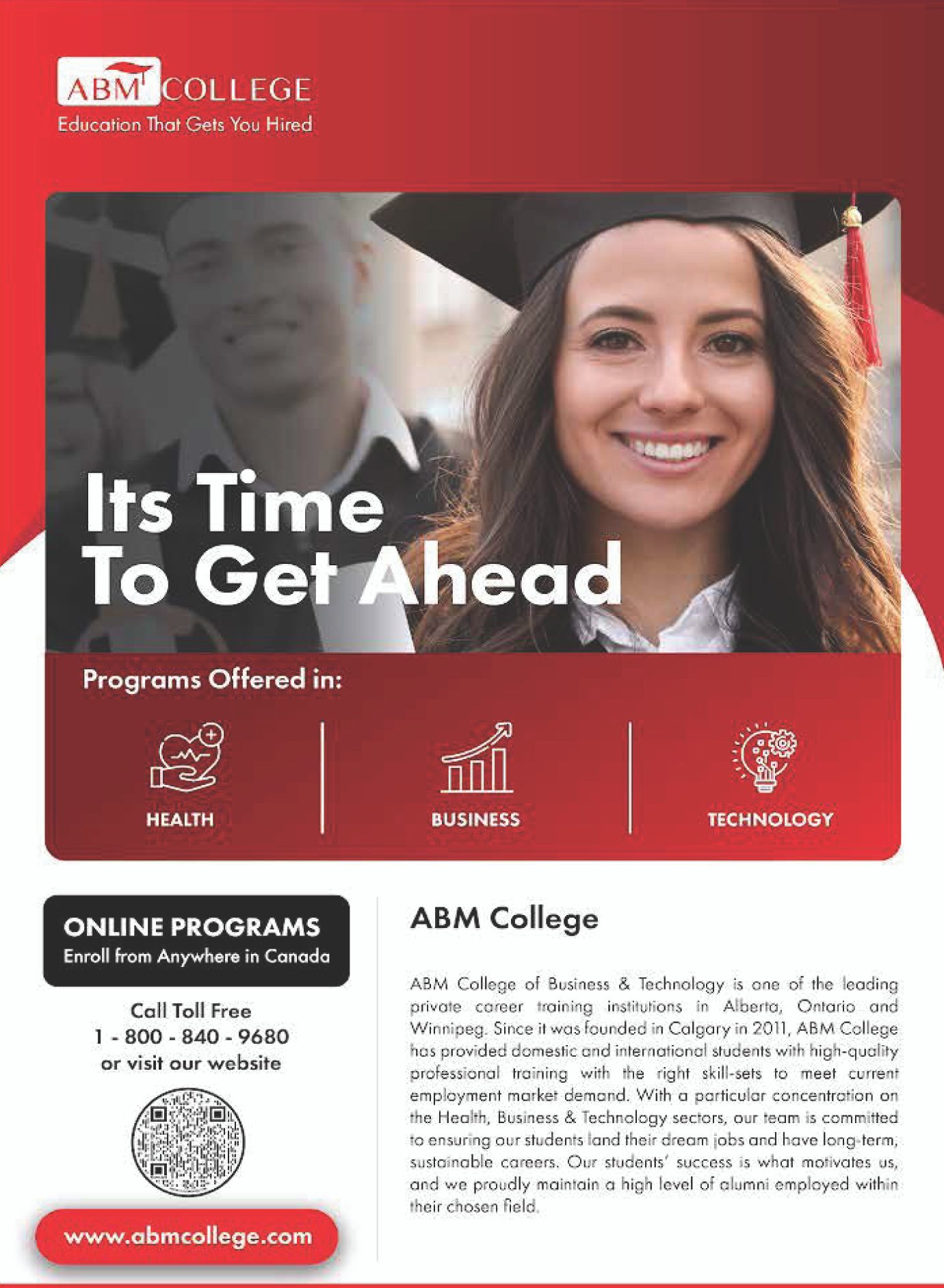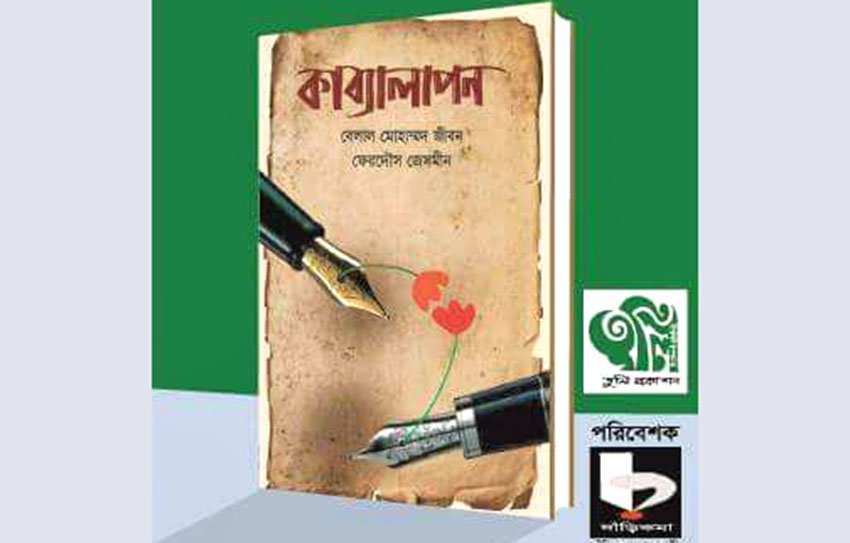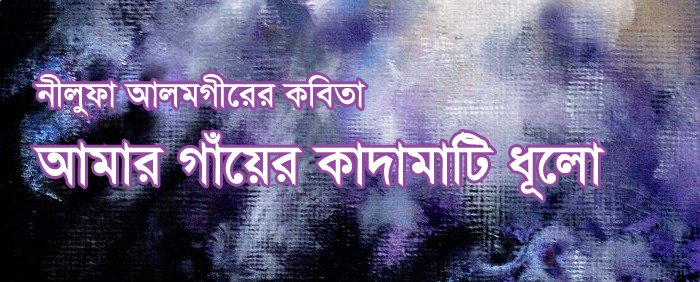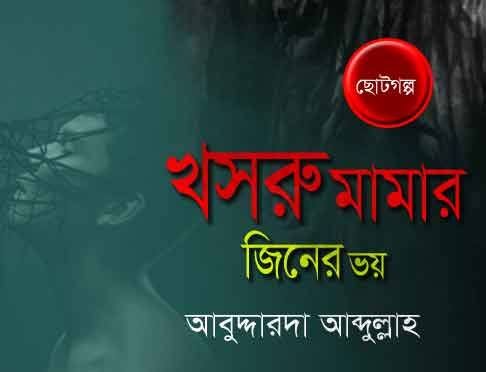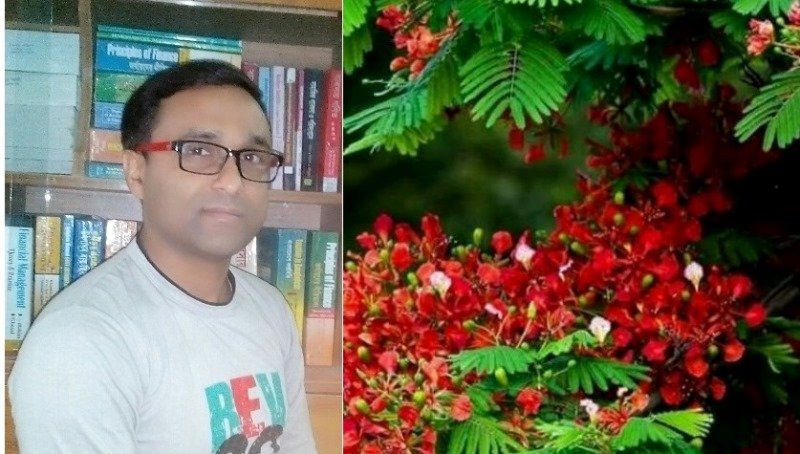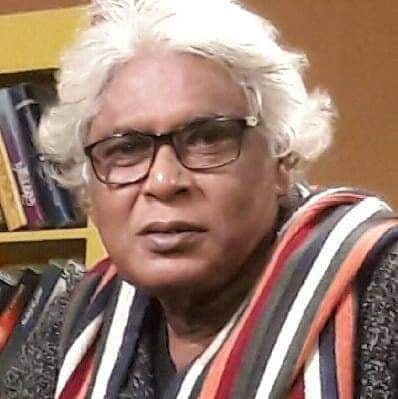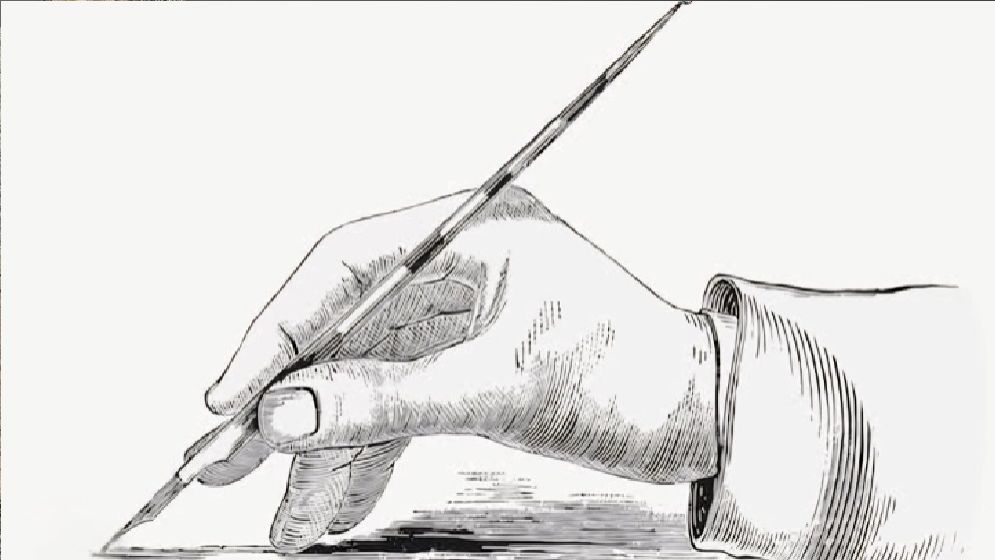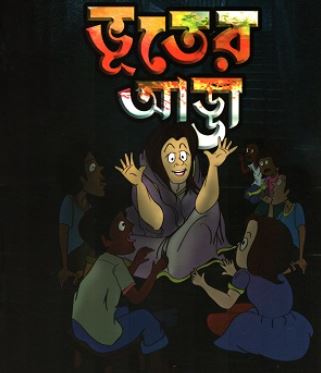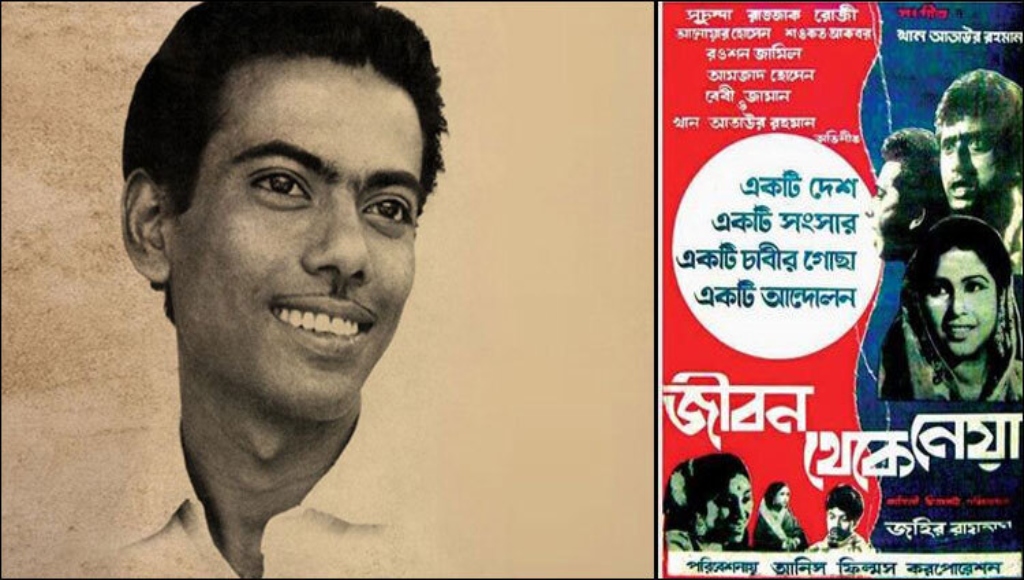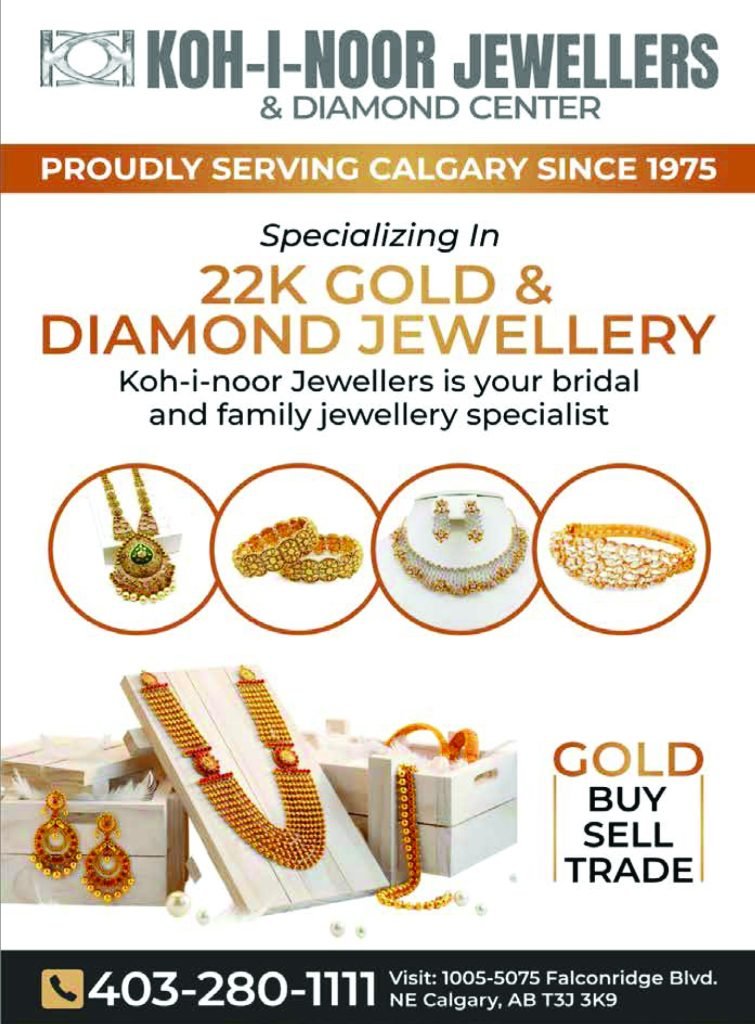প্রবাস বাংলা ভয়েস ডেস্ক :: পৃথিবী পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মানসিক বিবর্তনের পথ বেয়ে আধুনিক কবিতার জন্ম। মনোভূমির দ্বন্দ্ব, প্রক্ষেপ-প্রবণতা ও তার সংখ্যাতীত বিন্যাস এবং প্রতিবিন্যাস নিয়ে মানুষের মধ্যে দুটি প্রান্তিক অনুভব সতত সচল থাকে। যাপিত জীবনে এ অনুভাবনার একটি ব্যক্তির সুখানুভূতি এবং অন্যটি মর্মন্তুদ মনের দুঃখভার। সংবেদনশীল হৃদয়ের এ বেদনা যুগ থেকে যুগান্তরে সৃজনশীল মানুষকে বিবাগী করেছে হরষিত কিংবা বিষণ্নতার ঘোরে। অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম কবিমন (বাল্মীকি) তাই নিজের ভেতরের বিকশিত বাসনার ব্যাকুলতা থেকে গেয়ে উঠেছে-‘অলৌকিক আনন্দের ভার, বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার।’
রহস্যঘেরা অন্তর্লীন মনের এ মথিত যাতনা সবেগে সৃষ্টির প্রবাহে আলোকিত করছে শিল্প-সাহিত্যের আঙিনা। বিষাদ যখন জীবনকে অস্থির করে, ঠিক তখনই কবি প্রতিভার অসাধারণ উৎসারণ কর রেখায় হাঁক দিয়ে যায়-‘শান্তি কোথায় মোর বিশ্বভুবন মাঝে, অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে।’ আমরা জানি কবিতায় যেমন ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখ থাকে, তেমনি তাতে স্থান পায় সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। কালের প্রবাহে আদিকাল থেকে কবিতা নানা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়েছে দিনের পিঠে। খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকে ভারতবর্ষের মানুষ ধর্মবিশ্বাসী চেতনায় বৃত্তবন্দি। ফলে খুব প্রাচীনকালের কবিতার অঙ্গে সর্বাগ্রে স্থান পায় দেবতার গুণকীর্তন।
তারপর মধ্যযুগে সেই দেবনির্ভরতাকে সে সময়ের কবিরা কবিতার মধ্যে বাস্তবতার নির্যাস রাঙিয়ে তাতে আনন্দ তরঙ্গ ও আবেদনের কলতান সৃষ্টি করেন। কিন্তু তবুও কবিতার মধ্যে সত্যিকার মন্ময়তা ও তন্ময়তার পুলকিত স্পন্দন বার্তা থাকে নাগালের বাইরে। সঙ্গত কারণেই পাঠককে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে সার্থক কবিতার নোঙরের জন্য। ১৭৬০ সালের পর কবিতার নতুন মাত্রা পর্ব গণনা শুরু হয়। কাব্যজগতে আবির্ভাব ঘটে মাইকেল মধুসূধন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩)। মধ্যযুগীয় চেতনার অবসান ঘটিয়ে বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিকতা স্পষ্ট করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তার রচিত ‘ত্রিলোত্তমা সম্ভব’ (১৮৫৯) কাব্য, বাংলা কবিতার নতুন পথ নির্দেশ করে।
ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৮) গীতিকবিতার সূত্রপাত ঘটান। ঠিক তার পরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্যকে বিচিত্রমুখী করেন। সময়ের পিঠে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা কাব্যজগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবিতার শরীরে লাগে বহির্মুখী শিল্প-প্রকরণের ঢেউ। কবিতা সমালোচকদের আলোচনা চারদিকে প্রশাখা চারিয়ে দিয়ে বিশেষ একটি দিক উন্মোচিত করে। সেটি হলো শিল্প-নির্মাণের সীমাবদ্ধতাকে উতরিয়ে যাওয়ার স্পর্ধা। ত্রিশ-দশকের কবিতা তাই পাশ্চাত্য কাব্যভাবনাকে অনুসঙ্গ করে নতুন অবয়বে গতিশীল হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় কবিতা আকার-প্রকার ও শৈল্পিক বুননে যথার্থ দার্শনিক ভাবনায় শক্তিশালী কাঠামোয় প্রস্বরিত হতে থাকে। এ সময় থেকেই বিশ্বের প্রতিভাধর কবিরা নানামুখী দর্শন তথা মতবাদ দিয়ে কবিতার অঙ্গে বৈচিত্র্যময় মাত্রা প্রযুক্ত করে কাব্য নির্মাণের আকাশকে প্রসারিত করেন। ফলে হাল আমলে নতুন প্রকরণের বৈভবে দেশে দেশে অসংখ্য কবির সৃজনী প্রভায় পরিবর্তিত শৈল্পিক কৌশলে নির্মিত হচ্ছে কবিতা। ইউরোপ-আমেরিকার কবিদের হাতের কবিতা, নিত্য-নতুন কাব্যিক ব্যঞ্জনা গায়ে-গতরে মেখে অভিনব দৃষ্টিতে হাতছানি দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।
কবিতা তাই পূর্বের ‘প্রতীকী রূপ’ ছেড়ে ‘চেতনার প্রতীকী রূপ’ শরীরে ধারণ করতে শুরু করেছে। শিল্প হিসাবে কবিতা অনুভবের ও ভাবনার। আর এ ভাবনার ভরকেন্দ্রে স্থির হয়ে আছে ‘শব্দ।’ এস. টি কোলরীজের চিরায়ত মন্তব্য-’The best words in the best order’ গোটা বিশ্বে সমাদৃত। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কাব্য-সমালোচকরা এ অভিমতকে স্বীকারও করেছেন। কিন্তু তারপরও কোথায় যেন একটা অপূর্ণ রহস্যের মৌতাত ছড়িয়ে আছে অপরিহার্য শব্দবেষ্টিত কবিতায়। ফলে ‘শব্দ’ পরীক্ষা করে কবিতার তাৎপর্য নির্ণয়ের বেগটা ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দনি। কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডের তরুণ কবি স্টিভেন ওয়েলস বলেছেন-’Poetry is what looks like poetry, what sounds like poetry.’ অভিমতের সারকথা হলো- ‘যা পাঠে ও শ্রুতিতে গদ্যের মতো নয়, বক্তব্য সরাসরি নয়, ইঙ্গিতে প্রকাশিত-তাই কবিতা।’ এ সূত্রের বিচারে কবিতা নিয়ে, যা কিছু বলি না কেন-কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের তাগিদে আত্মগত চেতনার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এখানে শব্দ, ধ্বনি অথবা বাচ্য নয়, বাচ্যের অধিক ব্যঞ্জনাই কবিতার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে ভেতরের রহস্য কবিতার অপরিহার্য উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।
আধুনিক মানুষ বৈচিত্র্য-সন্ধানী ও বিচিত্রগামী। মানুষের হাতে সৃষ্ট কবিতা তাই নানারূপ অভিসারী বুনন চর্চায় অভিষিক্ত। চেতনাস্নাত মানব স্বাভাবিক চোখে দেখে, পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজ ও ইতিহাস প্রত্যেক কবির তৃষিত মনে সাবলীল মিলন অপরিহার্যতা কামনা করে। অসাধারণ প্রতিটি সফল কবিতা তাই স্বতঃপ্রণোদিত এবং দর্শনের চেতনাযুক্ত শিল্প। এ দর্শন চেতনা কল্পরূপ নির্ণয় জ্ঞাপক এবং বিজ্ঞান চেতনাযুক্ত। ফলে এ দর্শন বিজ্ঞানচেতনার প্রথম ধাপ। কবিতা নির্মাণের বেলায় দর্শন তাই চেতনার অনুষঙ্গ।
শব্দ কবিতার শরীর। কিন্তু জটিল পৃথিবীর সীমাহীন সমস্যা সবকিছুতে গভীর প্রভাব ফেলে। সীমাবদ্ধ এককবৃত্তে কবিতার ভাবকে কূল প্লাবিত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। ফলে প্রতিভাধর কবিরা সীমাবদ্ধতার মার্জিন ভেঙে কবিতার মধ্যে নানা মতবাদকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এবং একইসঙ্গে তাতে প্রয়োগ করেন ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ-কৌশলও। কবিতা প্রেকিক মাত্রই জানেন শব্দ ও অর্থ মিলেই হয় কবিতা। এ কারণে শরীরে প্রতিমার সঙ্গে কবিতার আত্মায় অর্থের ব্যঞ্জনা ঘটলে তা প্রবল আবেদনে সপ্রতিভ হয়ে ওঠে। কবিতার সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তাই ভূষণের প্রয়োজন যুগে যুগে অনস্বীকার্য হয়ে আসছে।
পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল মিলে উৎকৃষ্ট কবিতার সন্ধানে কবিরা কবিতার মধ্যে ব্যবহৃত-‘হিয়া, হেরি, মম, যবে, তবে’ শব্দকে বর্জনেরও জোরালো ইঙ্গিত দেন। শব্দ প্রয়োগে তাই মিতব্যায়িতা লক্ষণীয় ব্যাপার হয়ে ওঠে। বিষয়টি নিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষ কবিতায় লেখেন-‘ঘুরে ফিরে মনে হয়, বেশি কথা বলা হলো।’
প্রকরণ-শৈলীর পথ ধরে কবিতায় সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগ শুরু হয় দুর্বার গতিতে। একটি কবিতার উৎকর্ষ নির্ণয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইঙ্গিতবহ সাংকেতিক শব্দ বড় ভূমিকা পালন করে। অবশ্য এতে লক্ষণীয় বিষয় হলো কবিতার ভেতর ব্যবহৃত শব্দ পাঠকের কাছে যেন জটিল বা দুর্বোধ্য না হয়ে ওঠে। আধুনিক কবিতায় প্রতীকের ব্যবহার বহুল প্রচলিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা করতে প্রতীকের আশ্রয় নেন কবিরা। পাশ্চাত্যে এ প্রতীকী আন্দোলন গড়ে ওঠে, ফ্রান্সে উনিশ শতকের মধ্যভাগে। শার্ল বোদলেয়ারের লেখার মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।
কবিতার ভাবধারা ও নির্মাণশৈলীর সঙ্গে চিত্রকল্পের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। আধুনিক কবিতায় চিত্রকল্প ব্যাপক জায়গাজুড়ে আছে। বিশ শতকে লাওয়েল ও এজরা পাউন্ডসহ বিখ্যাত কবিরা কবিতার মধ্যে চিত্রকল্পকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছেন। দৃশ্যমান চিত্রকল্প ব্যবহারে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ফ্রস্ট ও রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নিজের শব্দমালা দিয়ে তারা সরল ও দৃশ্যমান চিত্রকল্প এঁকেছেন। যে কোনো সার্থক চিত্রকল্প কবিতাকে মালার মতো গেঁথে রাখে। কবিতাশৈলীর গুণগত মানে উচ্চায়ত মাত্রা পেতে সংবেদনশীল স্থানে চিত্রকল্প ব্যবহার হয়ে থাকে।
ত্রিশ দশকের বৈশ্বিক আবহ-স্নাত বাংলা কবিতা আধুনিকতার সব লক্ষণ নিয়ে হাজির হয়। বিষণ্ন পৃথিবীর বিক্ষিপ্ত হাওয়ার স্পর্শে এবং যুগ-সংকট অবলম্বন করে এ শিল্প সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বেগবান হতে থাকে। কবিতা বিধস্ত মানবতার ক্রন্দন ব্যথিত মনোভূমিতে বেদনার বেহাগ সৃষ্টি করে। টি, এস এলিয়ট লেখেন-
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper, (The Hollow Men)
এ পটভূমিতেই বহুদর্শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিশ্বাস্য মানসিক স্থিতিস্থাপকতা তাকে আধুনিক কবিতা নির্মাণের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করে। বলতে দ্বিধা নেই, তিনি এক-‘জীবন্ত চালচিত্র যার সামনে, যার প্রযত্নে ধীরে ধীরে নির্মিত হয়েছে আধুনিক কবিতার প্রতিমা, তার কায়া।’ বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী সময়ে নিদারুণ দুঃস্বপ্ন, অবসাদ এবং ব্যক্তির বহুমুখী টানাপোড়নে চূর্ণ হয়ে যায় পুরোনো বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। জীবনানন্দ দাশের ভাষায়-‘ইতিহাস এর মধ্যে কামাচ্ছন্ন, এখনো কালের কিনারায়।’
রবীন্দ্র-চেতনার আলো ঠিকরে পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ের তারুণ্যের ওপর। আবার একই সঙ্গে তার হাতে ধরা দেয় বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনাও। জীবনের প্রাত্যহিক জীর্ণতা তাকে বারবার বেদনার অমৃতপানে বাধ্য করে। কিন্তু কবি বিপদের চরমতম মুহূর্তেও স্বীয় প্রজ্ঞার আলোয় উত্তীর্ণ হয়েছেন ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে।’ যার প্রভাব কবিকাহিনি (১৮৭৮) কিশোর লগ্ন থেকে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত বিস্তৃত।
প্রবাস বাংলা ভয়েস /ঢাকা/ ২৩ এপ্রিল ২০২৫ /এমএম